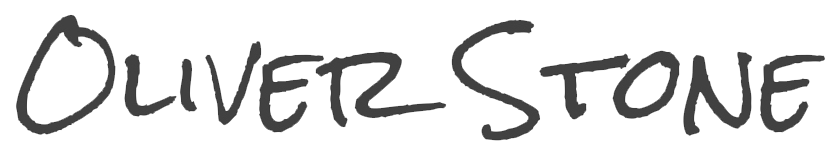বিশেষ লেখা—সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম/১
*ডঃ সচ্চিদানন্দ জোশী*
(লেখক এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস-এর সদস্য সচিব)
কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.):
“Mother, I bow to thee!
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Cool with the winds of delight,
Dark fields waving, Mother of might,
Mother free.
Glory of moonlight dreams
Over thy branches and lordly streams
Clad in the blossoming trees,
Mother, giver of ease,
Laughing low and sweet!
Mother, I kiss thy feet
Speaker sweet and low!
Mother to thee I bow.”
২০ নভেম্বর ১৯০৯-এ কর্মযোগীন-এ এই অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ২০ বছর আগেই ‘বন্দে মাতরম’ ভারতের ঐক্যের বীজ বপন করেছিল। মিছিল এবং ঘরে ঘরে গানটি ধ্বনিত হতে থাকে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং অঞ্চল নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে ঝড় তোলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই গান দেশকে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। ইংরেজিতে অরবিন্দের এই অনুবাদ নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে তোলে। স্বাধীনতার জন্য ভারতের কান্না গোটা বিশ্বের কাছে পৌঁছে যায়। ‘কর্মযোগীন’-এ এই গানের অনুবাদ শুধুমাত্র একটি অনুবাদ ছিল না, এটি একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল।
১৮৮৬-তে একটি স্তোত্র হিসেবে বন্দে মাতরম প্রথম মানুষের কানে পৌঁছায়। সেইসময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে একে সঙ্গীতের রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান। এর ১০ বছর পর ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ নিয়ে দেশ যখন উত্তাল, তখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত মাতার ছবি চিত্রায়িত করেন, যাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার প্রতিমূর্তি বলা যেতে পারে। যখন ব্রিটিশ শাসকরা ‘রানি দীর্ঘজীবী হোন’ গাইবার জন্য মানুষকে বাধ্য করছিলেন, তখন এক রাতের মধ্যেই এই স্তোত্রটি লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।
লাহোরে কংগ্রেসেও বন্দে মাতরম বিদ্রোহীদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। ভগত সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত এবং আরও অনেকে বন্দে মাতরম শ্লোগান দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজের সময় এই গানটিকে বাধ্যতামূলক করেন। মিছিল, কারাগার, জ্ঞানী-গুণী, কৃষক, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম ও বর্ণের মানুষ প্রার্থনা এবং প্রতিবাদের সময় এই গানটি গাইতে থাকেন।
শ্রী অরবিন্দ এটিকে প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এরপর বহু ভারতীয় ও ইংরেজিতে পারদর্শী ব্যক্তি গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। উর্দু সহ বহু ভারতীয় ভাষায় গানটির অনুবাদ করা হয়। ১৯০৬-এ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ব্রিটিশ আধিকারিক ডব্লু এইচ লী গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। প্রজন্ম এবং ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডি ছাড়িয়ে গানটি সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকের স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এই কাজের সুবাদে তিনি ব্রিটিশ সংগ্রহালয় এবং নথিপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন ঢাকা এবং উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৭৮০) ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে আনন্দমঠ উপন্যাস লেখেন। তবে এই উপন্যাসের আগে গানটি রচনা করেছিলেন তিনি।
১৮৭৫-এর ৭ নভেম্বর। দিনটি ছিল রবিবার। সেদিন অক্ষয় নবমীতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হাতে কলম তুলে নেন এবং বন্দে মাতরম গানটি লেখেন। অন্যরা যখন গানের মাধ্যমে রানির ভজনা করতেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাতৃভূমির জন্য এই গানটি গাইতেন। মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে লেখা গানটি শুধুমাত্র প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেনি, সেইসঙ্গে একটি প্রজন্মকে দেশপ্রেমে জাগ্রত করেছিল।
১৮৯৬-এ কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেন। এক দশকের মধ্যে ১৯০৫-এ স্বদেশী আন্দোলনের সময় গানটি বাংলার নানা প্রান্তে ধ্বনিত হতে থাকে। ব্রিটিশরা গানটিকে নিষিদ্ধ করে, ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়, প্রতিবাদকারীদের গ্রেফতার করা হয়। কলকাতায় স্কুল পড়ুয়ারা খালি পায়ে বৃষ্টিতে ভিজে গানটি গাইতে থাকে।
অরবিন্দ ঘোষ একে “ভারতের পুনর্জন্মের মন্ত্র” আখ্যা দেন। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকের মধ্যে বন্দে মাতরম সাহসের প্রতীক হয়ে ওঠে।
ভারতের স্বাধীনতা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। বন্দে মাতরম দেশবাসীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। তথাপি নতুন প্রজাতন্ত্রে কোন গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পাবে, তা নিয়ে গণপরিষদে বিতর্ক তৈরি হয়। ১৯৪৭-এ ‘জন গণ মন’-কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। অন্যদিকে, ‘বন্দে মাতরম’-কে জাতীয় স্তোত্র হিসেবে ঘোষণা করে সমমর্যাদা প্রদান করা হয়।
দেশ এখন ‘বন্দে মাতরম’ গানটির ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করছে। অন্যদিকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। বন্দে মাতরম-এ দেশের ঐক্য তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, স্বাধীনতার পর একে বাস্তবায়িত করেন সর্দার প্যাটেল। তিনি এককভাবে গোটা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর জন্যই আমাদের মাতৃভূমি আজ ‘সুজলা সুফলা’ হয়ে উঠেছে।
‘বন্দে মাতরম’ ভারতের চিরন্তন আবাহনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের গর্ব। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গানটি নতুন মাত্রা পায়। ১৯৫২তে হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় তৈরি হয় ‘আনন্দমঠ’ ছবিটি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম’ অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে।
এর অর্ধ শতাব্দী পরে ১৯৯৭-এ এ আর রহমানের ‘মা তুঝে সালাম’ গানটি গোটা বিশ্বকে নাড়া দেয়। হিন্দুস্তানের রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক সঙ্গীতের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ‘বন্দে মাতরম’-এর নব জাগরণ ঘটে। আজাদি কা মহোৎসব, স্কুলের প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রচারাভিযানের মতো বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার তরুণদের মধ্যে গানটিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।
চন্দ্রযান-৩ যখন চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে, তখন সামাজিক মাধ্যমে “চাঁদের মাটি থেকে বন্দে মাতরম” শব্দবন্ধটি ছড়িয়ে পড়ে। ‘বন্দে মাতরম’ কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস বা ভাবনার বিষয় নয়, এটি হল, মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের প্রতীক।
এই ভঙ্গুর সত্তার যুগে ‘বন্দে মাতরম’ আমাদের ঐক্যের বার্তা দেয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দেশাত্মবোধ কোনও আদর্শ নয়, এটি হল সহজাত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় এটি হল নদী, বনাঞ্চল এবং সন্তানদের রক্ষায় মায়ের প্রতি অঙ্গীকার। ২০২৫-এ নতুন আঙ্গিকে দেশ বন্দে মাতরম-এর ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করছে। গোটা দেশে ২২টি ভাষায় স্কুল পড়ুয়াদের কণ্ঠে গানটি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রযুক্তি এর পবিত্রতাকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি। বন্দে মাতরম রাজনৈতিক কবিতা নয়, এটি হচ্ছে একটি দর্শন।
‘বন্দে মাতরম’-এর মাধ্যমে আমাদের আত্মার পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক যুগের কারাগার থেকে অলিম্পিক স্টেডিয়াম, বাংলার নদী তীর থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ, সর্বত্র এটি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ১৮৭৫-এর অক্ষয় নবমীতে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বন্দে মাতরম’ রচনা করেছিলেন। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি, তাঁর এই গানই একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তাঁর স্তোত্র দেশবাসীর আত্মায় জায়গা করে নেবে।
আজ ভারত আবার নতুনভাবে জেগে উঠছে। আমাদের মাতৃভূমি আজ মুক্ত। শ্রী অরবিন্দ লিখেছেন : “For nations are not built by armies alone, but by those who can hear the voice of the Mother and bow to her with love.” আমাদের সন্তানদের এর যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। ‘বন্দে মাতরম’ হল আমাদের মা, আমরা তাঁর কাছে মাথা নত করি।
(ঋণ— প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার)।
---------------
হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক সেনগুপ্ত