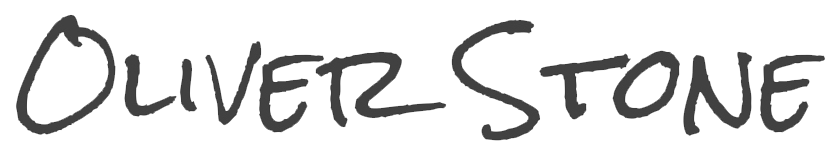কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে সাধক ভবানন্দের কন্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতের সার্ধশতবর্ষে সারা দেশে আলোড়ন উঠেছে । মল্লার-কাওয়ালী তালে ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত তাঁর সন্তান দলের কাছে গেয়েছিলেন।
ভবানন্দ আনন্দমঠে গানটি গাইবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে বসে সেকালের বিখ্যাত গায়ক ভাটপাড়ার পন্ডিত যদুনাথ ভট্টাচার্য সুরতাল যোগ করে গানটি প্রথম গেয়েছিলেন। ‘আনন্দমঠ’ যাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্র এটি লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বানী ছিল, এই গানে ‘বঙ্গদর্শন’-এর পেট না ভরলেও পঁচিশ বছর পর এ দেশের জনগণ ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতে মেতে উঠবে।
ভারতের জাতীয়তাবাদের উষাকালে দেশপ্রেমের যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছিল, তা আজও এই মন্ত্র উচ্চারণে এক অনাস্বাদিত দেশপ্রেমের আবেগকে জাগিয়ে তোলে। এটা কোনো রাজনীতির মন্ত্র নয়, কিন্তু ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্র উচ্চারণের সময় রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা অনেক সময় বিকৃত উচ্চারণ করে,যা দেশের জাতীয় আবেগের প্রতি অসম্মান করা হয়। এই সঙ্গীতে সমৃদ্ধশালী ‘ভারতমাতা’-র রূপ বর্ণনা আছে।
‘আনন্দমঠ’ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার অনেক আগে ১৮৭১সালে হিন্দু মেলার আদর্শে বারুইপুর মেলায় প্রথম ভারতমাতার মূর্তি দশভূজা উন্নতি দেবীর রূপকল্পে নির্মাণ করা হয়। মায়ের দশ হাতে দশ অস্ত্র বলতে কৃষি, উদ্যানতত্ত্ব, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যায়াম , সাহিত্য, প্রতিযোগিতা, সামাজিক সংস্কার, আত্ম নির্ভরতা, এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষার শপথ নেওয়া হয়।
সিংহের পিঠে উন্নতি দেবীর অধিষ্ঠান। সিংহ উদ্যম ও সাহসিকতার প্রতীক। উন্নতি দেবীর পুজোয় চব্বিশ পরগনা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সবাই এসেছিল। দেশপ্রেমের আবেগে জাত ধর্মের অহঙ্কার মানুষের ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ‘বন্দেমাতরম্’ হিন্দু মুসলিম বিভাজনের সাম্প্রদায়িকতার অভিসন্ধি মাথায় নিয়ে লেখেননি।
স্থুল, সুক্ষ ভাবে ভারতমাতার প্রতি ভালোবাসা, এবং এদেশের জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্রর। ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্র উচ্চারণের জন্য বরিশাল কংগ্রেস প্রাদেশিক অধিবেশনে সুশীল গুহ ঠাকুরতা আঠারো ঘা বেতের তীব্র অত্যাচার সহ্য করতে ভয় পায় নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে একদিনের জেল খেটেছেন।
একসময় আমাদের দেশে মুসলিম লীগের সাথে অতি প্রগতিবাদীরা ‘বন্দেমাতরম্’কে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট বলে সমালোচনা করেছিল। তার উত্তর দিয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলার বিশিষ্ট পন্ডিত রেজাউল করিম। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। মুসলিম লীগের সভায় যখন আনন্দমঠের কপি পোড়ানো হচ্ছে তখন জ্ঞানবৈরী সাম্প্রদায়িক লীগ শক্তির বিরোধীতা করতে এই জ্ঞানতপস্বী পথে নেমেছিলেন।
তিনি লিখলেন অহিন্দু দৃষ্টিতে বঙ্কিম প্রতিভা। করিম সাহেব বলেছিলেন, ‘বন্দে মাতরম্’-এ যে ভারতমাতার গৌরবগাথা বর্ণনা করা হয়েছে তা নিছক কোনো হিন্দু দেবীর মূর্তি নয়। তার মধ্যে আছে ভারতমাতার অবয়ব। ইংরেজ শাসনের সময় বিশ শতকে যাঁর বই রাজরোষে প্রথম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ১৯০৮ সালে সেই কবি সৈয়দ আবু ইসমাইল সিরাজি তাঁর ‘অনল প্রবাহ’ কাব্য গ্রন্থে ভারতমাতার রূপ বর্ণনা করেছিলেন।
দশপ্রহরণধারিণী ভারত মাতা কৃষি শিল্প, শিক্ষা, সঙ্গীত, নাটক, শিল্পচর্চা, বিজ্ঞানসহ দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনা করেছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতে। রেজাউল করিমের ভাষায় বলতে হয় ‘বন্দে মাতরম’ কোনো সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গীত নয়। ফরাসি জাতীয় সঙ্গীত ‘ল্যা ম্যার্সেলিশ’-এর সাথে এর তুলনা করা যায়। অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ সালে ‘কর্মযোগীন’ পত্রিকায় ‘বন্দে মাতরম্’-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে পেয়েছেন ‘vison of mother’।
অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের জাতিসত্ত্বার ইতিহাসে ‘বন্দে মাতরম্’ প্রথম জাতীয় সংস্কৃতির রূপকল্প নির্মাণ করেছিলো। যার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি বুঝতে শিখেছিলো তার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি ঐতিহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে পথ দেখালেন জাতীয়তাবাদের আলোকে।
(প্রাবন্ধিক, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধীন রাজগীরের রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সম্পাদক)
---------------
হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক সেনগুপ্ত