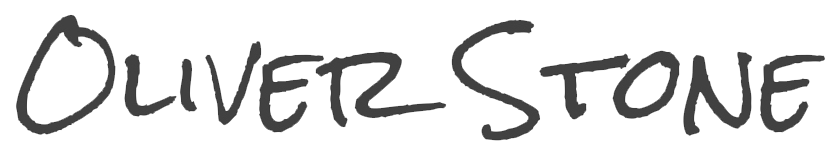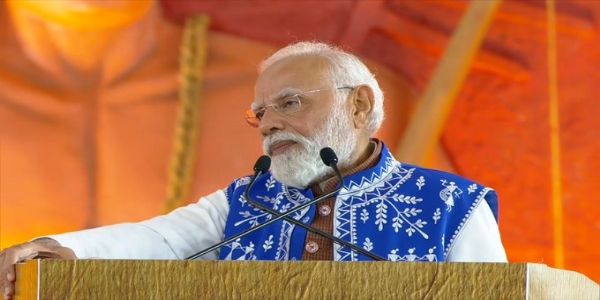কলকাতা, ১৯ নভেম্বর, (হি.স.): “আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী এক ব্রিটিশ সেনার হাতে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়ার পর হেনস্থা-বিধ্বস্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধী-চেতনা ও অধ্যাত্মপোলব্ধিতে শ্মশানকালীরূপে ধ্যানদর্শন দেন দেশমাতৃকা। যার পর রচিত হয় ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রগীত।” ‘বন্দে মাতরম’-এর সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে এ কথা জানালেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিংএর প্রাক্তন শিক্ষক, বহুজাতিক সংস্থার প্রাক্তন চাকুরে, দেবযানী ভট্টাচার্য।
তিনি জানিয়েছেন, “এতদ্পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে ‘বন্দে মাতরম’ প্রকৃতই এক দৈব মন্ত্রগীত হিসেবে প্রতীত হয়, যার রচনাকার্যের মাধ্যমে শুভসূচনা হয়েছিল এক পুণ্যযজ্ঞের এবং যে মন্ত্রের অপরিসীম শক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে জন্ম দিয়েছিল এক সমাজবিপ্লবের।
১৮৮২ সালে ‘আনন্দমঠ’ রচনা-পরবর্তী ঘটনাক্রম যে অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়, দৈব ইচ্ছা বিনে তা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। ১৮৮২ সালেই রেভারেন্ড হেস্টির প্রকাশ্য হিন্দুবিদ্বেষ ‘বন্দে মাতরম’ বীজমন্ত্রকে আত্মস্থ করতে ভারতীয়দের করেছিল পরোক্ষ সাহায্য।”
ব্যবস্থাপনা প্রশাসক, উদ্যোগপতি দেবযানীর কথায়, “অতঃপর ১৮৮৫ সালেই ‘বন্দে মাতরম’ গানে সুরারোপ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সে বছরেই ‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে জন্ম হয় ঔপনিবেশিকতাবিরোধী জাতীয়তাবাদের।
‘বন্দে মাতরম’ গান যেন ছিল তার সূচনামন্ত্র। সেই একই কালখণ্ডে নরেন্দ্রনাথ দত্তের মেধা ও অধ্যাত্মচেতনাকে মনের মত রূপদান করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব যার পর, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই সেই সময় যখন কন্যাকুমারীস্থ শিলার উপর উপবেশনরত অবস্থায় বিবেকানন্দের ভাবজগতেও ভারতরাষ্ট্র ও তার ধর্ম এক ও অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় ঠিক যে প্রকারে বন্দে মাতরম রচয়িতার উপলব্ধিতেও জন্মভূমি হয়ে উঠেছিলেন পূজ্যা দেবীমাতৃকা।
বঙ্কিমের ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্র যখন বঙ্গের মানুষের হৃদয়তন্ত্রে তুলছে ঝঙ্কার, ভারত পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দও তখন পৌঁছচ্ছেন অনুরূপ উপলব্ধিতে। এ সকল সংযোগে দৈবিকতার ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রের উদগাতা জন্ম দিয়েছিলেন যে আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের তাকেই বৈদান্তিক বিশ্বমানবতার স্তরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।”
লেখক, কলামলেখক দেবযানীর কথায়, “এ হেন বীর সন্ন্যাসীর ভাবনায়ও ‘বন্দে মাতরম’ ছিল ভারতঐক্যের মন্ত্রসূত্র। আবার সেই একই সময়ে, ১৮৯৬’এ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে, ‘বন্দে মাতরম’ গানটিই নিজ কণ্ঠে পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এইভাবেই, ১৮৭৫’এর রচনালগ্নের পর থেকে, গোটা ভারতবর্ষকে ধীরে ধীরে, পাকে পাকে, নিজশক্তিতে আবিষ্ট করেছে বন্দে মাতরম নামক দৈবমন্ত্র।
যে ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ করেন পাশ্চাত্যযাত্রা, সেই বছরেই ইংল্যান্ডের পাট চুকিয়ে আইসিএসের কারিকুলাম অসমাপ্ত রেখে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন অরবিন্দ ঘোষ, ‘বন্দে মাতরম’কে যিনি করে তুলেছিলেন মহাবিপ্লবের আধ্যাত্মিক উদ্ঘোষ।”
রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেবযানীর কথায়, “মূলতঃ অরবিন্দ ঘোষের মাধ্যমেই ‘স্বদেশী আন্দোলন’এর সময় ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রগীতের কম্পাঙ্ক ভারতের জনসমুদ্রে তুলেছিল জাতীয়তাবাদের সুনামি। সেই সঙ্গে এ-ও উল্লেখ্য যে ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্র আবিষ্ট করেছিল কেবলমাত্র ভারতীয়দের নয়, শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদেরকেও।
‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রের উচ্চারণকে নিষিদ্ধ করা এবং ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকার উপর রাজদ্রোহের মামলা ঠোকার মাধ্যমে তাদের নিজেদের উপর ‘বন্দে মাতরম’এর অপরিসীম প্রভাবের নেতিবাচক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল বৃটিশ সরকার। এ-ও ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রের দৈবত্বেরই অপর এক প্রমাণ ভিন্ন নয়।”
---------------
হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক সেনগুপ্ত