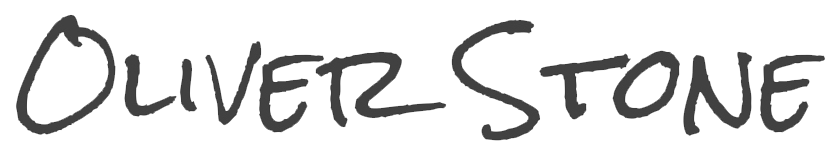কলকাতা, ৪ অক্টোবর, (হি.স.): অবিভক্ত বাংলার দুর্গাপুজো ইতিহাসে সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন পাওয়া যায় কোচবিহার রাজপরিবারের মধ্যে। মহারাজা নরনারায়ণের সময় (১৬শ শতক) থেকে এখানে দুর্গাপুজো শুরু হয়। উৎসসন্ধানে এ কথা জানিয়েছেন
কলকাতা হাইকোর্ট, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের প্রশাসনিক আধিকারিক রাহুল বণিক।
রাহুলবাবু জানিয়েছেন, “দেবীকে রাজশক্তি ও রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে পূজা করা হতো এবং সৈন্য ও প্রজাদের উপস্থিতিতে তা মহাসমারোহে পালিত হতো। প্রায় একই সময়ে নবদ্বীপে শোভারাম মজুমদারের দুর্গাপুজো (১৬০৬ খ্রিঃ) বাংলার প্রথম সার্বজনীন ধাঁচের জমিদারী পুজো হিসেবে পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।
বাংলাদেশের দিনাজপুর রাজবাড়ির পুজো ১৭শ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেবীর পূজা এখানে আজও বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রাজপুজো। একই শতকে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতেও দুর্গাপুজো শুরু হয়, যেখানে প্রথমদিকে বলিপ্রথা প্রচলিত ছিল। এটি উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক রাজশক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। একই সময়ে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো মহার্ঘ আয়োজন ও সোনার গহনায় দেবীর সজ্জার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।
এরপর রাজধানী কলকাতায় একাধিক জমিদার ও রাজপরিবারের পুজো ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শোভাবাজার রাজবাড়ি। রাজা নবকৃষ্ণ দেব ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এই পুজো শুরু করেন। এই পূজোতে একদিকে ছিল ইংরেজদের আতিথেয়তা, অন্যদিকে বাঙালি সমাজের মধ্যে ঐশ্বর্য প্রদর্শনের নিদর্শন। শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো কলকাতার ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে আজও টিকে আছে।
এছাড়া লাটসাহেবের বাড়ি বা শোভাবাজার রাজবাড়ির দ্বিতীয় প্রাসাদ, সিমলা রাজবাড়ির পূজো (শোভারাম বসাকের পরিবার), চোরবাগানের দত্ত পরিবারের পূজো, এবং পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির পূজো—সব ক’টিই ১৮শ শতকের শেষ থেকে ১৯শ শতকে গড়ে ওঠে। এগুলো কেবল পূজা নয়, বরং ইংরেজ শাসনের যুগে বাঙালি জমিদার সমাজের প্রাচুর্য, রাজনীতি এবং সামাজিক মর্যাদার প্রদর্শনীর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।
সব মিলিয়ে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের রাজপুজো (কোচবিহার, বৈকুণ্ঠপুর, দিনাজপুর) ছিল আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রতীক; নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের পূজো (শোভারাম মজুমদার, কাশিমবাজার) ছিল জমিদারি ঐতিহ্যের পথিকৃৎ; আর কলকাতার রাজবাড়ির পূজোগুলো মূলত ছিল নগরায়িত বাংলার ঐশ্বর্য, রাজনৈতিক প্রভাব ও সামাজিক প্রদর্শনের প্রতিফলন। এই ধারাই একত্রে অবিভক্ত বাংলার দুর্গাপুজোকে বহুমাত্রিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।”
---------------
হিন্দুস্থান সমাচার / মৌসুমী সেনগুপ্ত