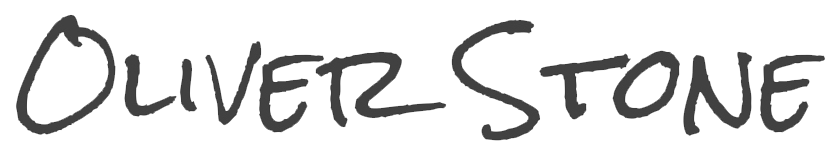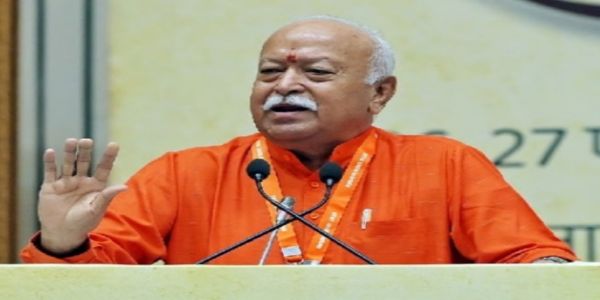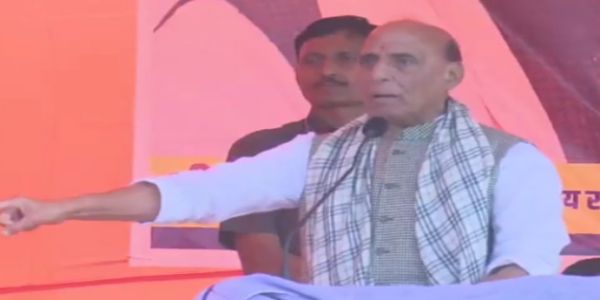বিশেষ লেখা—সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম/৪
গৌতম ভট্টাচার্য
(প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট, আর্থ সামাজিক বিষয়ের বিশ্লেষক)
কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.): অনেক সময়ই ‘বন্দে মাতরম’ গানটি নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে দেশমাতৃকার যে রূপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি কি ‘বঙ্গমাতা’র না ‘ভারতমাতা’র?
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বন্দে মাতরম’এর ভূমিকা কী ছিল, সে বিষয়ে আমরা সকলেই জানি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গানটিকে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে (১৮৮২) অন্তর্ভুক্ত করেন। সাহিত্যসম্রাটের সাড়া জাগানো উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’, বইয়ের আকারে ১৮৮২তে প্রকাশিত হলেও কাহিনিটির প্রেক্ষাপটটি ছিল আরো একশো বছর আগেকার, বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ফকির- সন্ন্যসী আন্দোলন।
গানটিতে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় স্তবকে উল্লেখ করেছেন, “সপ্তকোটিকণ্ঠ কল-কল নিনাদকরালে …” । ভারতবর্ষের প্রথম সেনসাসে (১৮৭২) অবিভক্ত বঙ্গদেশের জনসংখ্যা দেখা যাচ্ছে সাত কোটির কিছু বেশী। তাই মনে হয় সপ্তকোটিকণ্ঠ যখন, নিশ্চয়ই সৃষ্টিকার তখন বঙ্গমাতার রূপই চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টিকার যা চিন্তা করেই লিখুন না কেন, জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৮৯৬) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন গানটি নিজের সুরে পরিবেশন করেন সেই থেকেই গানটির ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ রূপে পাল্টিয়ে যায়। আমারও ‘বন্দে-মাতরম’কে ভারতমাতার বন্দনা ভাবতেই ভালো লাগে। হয়তো আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষেও তাই।
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুরকার বন্দে- মাতরমে সুরারোপ করেন - যদু ভট্ট, রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর ও বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কার, তিমিরবরণ, হেমন্ত মুখার্জি, রবিশঙ্কর, এ.আর.রহমান প্রমুখ। রাষ্ট্রগীত হিসেবে গানটির সুরের কোনো আদর্শ সংস্করণের (স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন) উল্লেখ নেই।
বঙ্কিমচন্দ্র সুরকার ছিলেন না। যখন তিনি কবিতা হিসেবে বন্দে-মাতরম লিখেছিলেন, সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেন নি তাঁর সৃষ্টির কিরকম সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভবিষ্যতে হবে! - তবে স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন না থাকার জ্বালাও আছে। ইউ-টিউবে এক গায়িকাকে দেখলাম বন্দে-মাতরমের সুরেও সামান্য পরিবর্তন করে দিতে। ‘সপ্তকোটিকণ্ঠ’কে তিনি গাইলেন কোটিকোটিকণ্ঠ আর ‘দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে’ হয়ে গেছে কোটিকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে ! - এই পরিবর্তন মানতে অসুবিধা হয়!
ছোটবেলা মা’র মুখে শুনেছি কিভাবে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা কংগ্রেসী আন্দোলনকারীদের ব্রিটিশ রাজের পুলিশ লাঠির বাড়ি দিতে দিতে ভ্যানে তুলছে, তবুও তাঁরা জোর গলায় বলে চলেছে “বন্দে মাতরম”! … আবার এও শুনেছি কিভাবে ছেচল্লিশের দাঙ্গায় যুযুধান দুই পক্ষ হাড় হিম করা স্লোগান তুলেছে - একদিকে “আল্লাহু আকবর”, অন্য দিকে “বন্দে-মাতরম”!
এটাও ঠিক, ‘বন্দে মাতরম’-এ দেশমাতৃকার যে সাকার রূপটির বন্দনা করা হয়েছে কট্টরবাদী মুসলমানদের মতে সেটা ইসলাম বিরোধী। তাই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন ‘বন্দে-মাতরম’ গাওয়া ‘চাপিয়ে দেবার’ বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধ্যানধারণা থেকে উত্তরণের প্রয়াজন আছে। বন্দে-মাতরমের স্পিরিটটা বুঝতে পারলে বোধ হয় এই ধরণের সমস্যা থাকতো না।
---------------
হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক সেনগুপ্ত